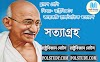Judicial Review
বিচার বিভাগীয় সমীক্ষা
দ্বাদশ শ্রেণি।। রাষ্ট্রবিজ্ঞানসরকারের বিভিন্ন বিভাগ
[West Bengal Council of Higher Secondary Examination (WBCHSE) Class 12 Political Science Questions and Answers in Bengali; Chapter- Organs of Government; Question- Judicial Review.]
প্রশ্ন- বিচারবিভাগীয় সমীক্ষা বলতে কী বােঝ? বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা কীভাবে সংরক্ষিত হয় তা ব্যাখ্যা করো৷ [2+6]
উত্তর- বিচারবিভাগীয় সমীক্ষা (Judicial Review) হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বিচারবিভাগ শাসনবিভাগ এবং আইনবিভাগের কাজের পর্যালোচনা করতে পারে। বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার অধিকারী কোনো আদালত আইনসভা প্রণীত কোনো আইন বা শাসনবিভাগের কোনো নির্দেশের বৈধতা বিচার করতে পারে। সবদিক বিচার করে যদি দেখা যায় উক্ত আইন বা নির্দেশটি সংবিধানবিরোধী, তবে আদালত সেই আইন বা নির্দেশকে বাতিল করে দিতে পারে। এইভাবে, বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার মাধ্যমে বিচারবিভাগ সরকারের অপর দুই বিভাগকে অর্থাৎ শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।
বিচারবিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায়
আধুনিক রাষ্ট্রে সরকারের প্রধান তিনটি স্তম্ভ হল- 1) আইনবিভাগ, 2) শাসনবিভাগ এবং 3) বিচারবিভাগ। বিচারবিভাগের কাজ হল ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা যা সরকারের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে, গণতন্ত্রের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ বিচারালয়ের উপর। কিন্তু বেশিরভাগ রাষ্ট্রে বিচারবিভাগের উপর আইনবিভাগ এবং শাসনবিভাগের নিয়ন্ত্রণ থাকে। আবার, যে সকল রাষ্ট্রে ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রযুক্ত হয়েছে, সেখানেও নানা কারণে বিচারবিভাগের স্বাধীনতা এবং নিরপেক্ষতা নিয়ে অনেকসময় প্রশ্ন উঠে।
বিচারবিভাগের স্বাধীনতা কীভাবে সুরক্ষিত রাখা যায়, সেবিষয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্ন মত পোষণ করেন। তবে, সামগ্রিকভাবে বিচারবিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায়গুলি হল এরকম-
1) যোগ্য বিচারপতি নিয়োগ
সুষ্ঠুভাবে বিচারকার্য সম্পন্ন করা একটি গুরুদায়িত্ব বিশেষ। তাই একজন অযোগ্য এবং অক্ষম ব্যক্তিকে বিচারপতি পদে নিয়োগ করা কখনোই কাম্য নয়। সেজন্য সংবিধানে উল্লেখিত অথবা আইনসভা প্রণীত নির্দিষ্ট যোগ্যতা অনুসারে বিচারপতি নিয়োগ করা উচিত।
2) স্বচ্ছ নিয়োগ পদ্ধতি
বিচারপতি নিয়োগের তিন রকম পদ্ধতি রয়েছে। বিচারপতিরা 1) জনগণ কর্তৃক বা 2) আইনসভা কর্তৃক অথবা 3) শাসনবিভাগ কর্তৃক নির্বাচিত হতে পারেন। সব পদ্ধতিরই কিছু নেতিবাচক দিক রয়েছে। বিশেষ করে জনগণ দ্বারা বিচারপতি নিয়োগের পদ্ধতিটি একেবারেই যথার্থ নয় বলে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মত প্রকাশ করেছেন। আইনবিভাগ অথবা শাসনবিভাগের দ্বারা বিচারপতি নিয়োগ করাটাই যুক্তিযুক্ত। তবে, প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত কোনো ব্যক্তিকে বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ করা কখনোই কাম্য নয়।
3) কার্যকাল নির্দিষ্টকরণ
বিচারপতিদের কার্যকালের স্থিরতা থাকা প্রয়োজন। নিজেদের কার্যকালের মেয়াদ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকলে তারা নিশ্চিন্তমনে বিচারকার্য সম্পন্ন করতে পারবেন।
4) অপসারণ পদ্ধতির স্বচ্ছতা
সংবিধানে উল্লেখিত নির্দিষ্ট আইন অনুসারে অথবা উপযুক্ত আইনসভা প্রণীত আইন অনুসারে বিচারপতিদের অপসারণ হওয়া উচিত। বেশিরভাগ রাষ্ট্রেই বিচারবিভাগ অন্য দুই বিভাগের থেকে কম শক্তিশালী হয়। তাই বিচারপতিদের অপসারণের নির্দিষ্ট পদ্ধতির উল্লেখ না থাকলে আইনবিভাগ এবং শাসনবিভাগ নিজেদের স্বার্থে যোগ্য এবং ন্যায়পরায়ণ বিচারপতিকেও অপসারণ করে দিতে পারে।
5) পর্যাপ্ত বেতন ও ভাতা প্রদান
বিচারপতিদের বেতন এবং ভাতা এতটাই হওয়া উচিত যাতে তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য অন্য কোনো কর্মে নিযুক্ত হতে না হয়। একইসঙ্গে, তাদের বেতন এবং ভাতার বিষয়টি যেন আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের এক্তিয়ারের বাইরে থাকে। সহজভাবে বললে, কোনো বিচারপতিকে যদি পরিবারের ভরণপোষণ করার জন্য চিন্তা করতে হয়, তাহলে বিচারকার্য ব্যাহত হবেই। আবার, পর্যাপ্ত বেতন ও ভাতা না পেলে তারা আর্থিক প্রলোভনের ফাঁদে পা দিতেও পারেন। সেক্ষেত্রেও ন্যায় প্রতিষ্ঠা হবে না, বরং বিচারের নামে প্রহসন হবে।
6) স্বতন্ত্রীকরণ
বিচারবিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার সবথেকে বড় উপায় হল বিচারবিভাগকে আইনবিভাগ এবং শাসনবিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করতে হবে। বিচারপতিদের নিয়োগ, বদলি এবং পদচ্যুতির বিষয়ে আইনবিভাগ এবং শাসনবিভাগ যেন হস্তক্ষেপ করতে না পারে। উক্ত দুই বিভাগ থেকে বিচারবিভাগকে স্বতন্ত্র করতে পারলে বিচারবিভাগের স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনতা রক্ষিত হতে পারে।
পরিশেষে বলা যায়, উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিচারবিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করা খুব একটা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। বিচারবিভাগের উপর অপর দুই বিভাগের কমবেশি নিয়ন্ত্রণ থাকবেই। তবে, যেসব রাষ্ট্রে ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ নীতি গৃহীত হয়েছে সেখানে এই হস্তক্ষেপ কম হবে, আর যেখানে ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ নীতি গৃহীত হয়নি সেখানে হস্তক্ষেপের পরিমাণ বেশি হবে।